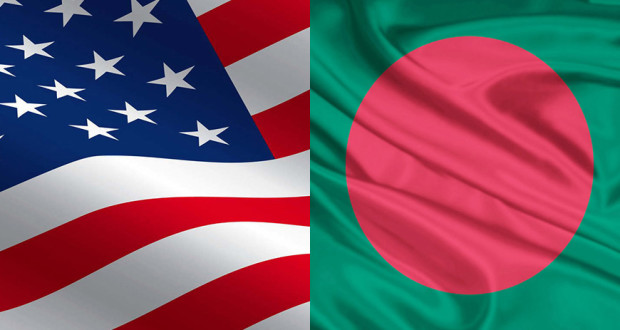১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে আমার বাবা শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৬-দফা দাবি পেশ করেন। ঢাকায় ফিরে ৬-দফার সমর্থনে জনমত তৈরি করতে সারা দেশে তিনি সভা-সমাবেশ করা শুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যে ৬-দফার পক্ষে ব্যাপক গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। স্বৈরশাসক আইয়ুব খান ভীত হয়ে পড়েন। শেখ মুজিবকে রুখতে হবে। তিন মাসের মধ্যে বাবাকে আট বার গ্রেফতার করা হলো। আমার ‘মা’ সব সময় একটা সুটকেস ও বিছানাপত্র গুছিয়ে রাখতেন। বাবাকে গ্রেফতারের আগেই থানা থেকে পুলিশের ফোন আসত, ‘স্যার, আমরা আপনাকে অ্যারেস্ট করতে আসছি।’ বাবা বলতেন, ‘আসুন।’
বাবা ফোনটা রেখে মাকে সবকিছু গুছিয়ে হাতের কাছে রাখতে বলতেন। তারপরেই বাবা একটা ফোন করতেন তাজউদ্দীন চাচাকে, ‘তাজউদ্দীন রেডি হও। আমাকে নিতে আসছে, তোমার কাছেও যাবে।’ হাসিনা আপা মাঝেমধ্যে বিদ্রোহ করতেন। কিছুতেই পুলিশকে বাসায় ঢুকতে দেবেন না; যেতে দেবেন না বাবাকে।
বাবা হেসে বলতেন, ‘যেতে তো হবেই।’ তবে মা ঘাবড়াতেন না কখনই। কেবল মুখটা বিবর্ণ ও মলিন হয়ে যেত। অন্যভাবেও বোঝা যেত তার কষ্ট। বাবা যতদিন জেলে থাকতেন, ততদিন মা একটা ভালো বা রঙিন শাড়ি পরতেন না। বাবা বাড়ি ফেরার পর সব আবার ঠিক হয়ে যেত আগের মতো।
স্কুলে কোনো অনুষ্ঠানে অভিভাবক হিসেবে মা-ই যেতেন; সঙ্গে কামাল ভাই। বেশির ভাগ সময় জেলে থাকার কারণে বাবা কখনো যেতে পারতেন না। অনেক অভিভাবক তাদের বাচ্চাদের আমাদের সঙ্গে মিশতে বারণ করতেন, আমাদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে বলতেন। আবার অনেকে স্নেহ-আদর দিয়ে কুশলাদি জানতে চাইতেন।
রাজনৈতিক পরিবারগুলোর জীবনযাপন অন্যসব পরিবার থেকে একটু আলাদা। তার ওপর শেখ সাহেবের সন্তান বলেই আরো আলাদা ছিল আমাদের ভাইবোনদের জীবন। কামাল ভাই বেশ বড় হয়েও জানতেন না, ‘বাবা’ কী বা কাকে বলে!
আব্বার লেখা ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’তে এই বিষয়টা খুবই হূদয়স্পর্শী ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। সেখান থেকে একটুখানি উদ্ধৃতি দিচ্ছি, যারা পড়েননি তাদের জন্য। বাবার কথায়—“একদিন সকালে আমি ও রেণু বিছানায় বসে গল্প করছিলাম। হাসু ও কামাল নিচে খেলছিল। হাসু মাঝে মাঝে খেলা ফেলে আমার কাছে আসে আর ‘আব্বা’, ‘আব্বা’ বলে ডাকে। কামাল চেয়ে থাকে। এক সময় কামাল হাসিনাকে বলছে, ‘হাসু আপা, হাসু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।’ আমি আর রেণু দুজনই শুনলাম। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে যেয়ে ওকে কোলে নিয়ে বললাম, ‘আমি তো তোমারও আব্বা।’ এমনিতে কামাল আমার কাছে আসতে চাইত না। আজ গলা ধরে পড়ে রইল। বুঝতে পারলাম, এখন আর ও সহ্য করতে পারছে না।”
মাঝেমধ্যে আমার মনে হয়, আমার বাবা যদি রাজনীতি না করে শুধু লেখালেখি করতেন, তাহলে হয়তো সেরা লেখকদের সারিতে স্থান করে নিতেন। এত সুন্দর, সহজ-সরল, সাবলীল তার ভাষা, যার তুলনা হয় না।
জীবন চলার পথে অনেক কঠিন বাস্তবতা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে সবকিছু সহজভাবে গ্রহণ করার। বাবা তখন জেলে। কামাল ভাই ঢাকা কলেজে ভর্তি হবেন। কিন্তু মোনায়েম খানের হুকুম, কিছুতেই শেখ মুজিবের ছেলেকে ঢাকা কলেজে ভর্তি করা যাবে না।
মা প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে ফোন করলেন। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন, ‘মা, তুমি ফোন করেছ, আমার চাকরি যায় যাক, কিন্তু আমি কামালকে ভর্তি করিয়ে নেব। ওর স্কুল থেকে প্রধান শিক্ষক মামুন সাহেব প্রশংসা করে সার্টিফিকেট দিয়েছে, আমি অবশ্যই ভর্তি করিয়ে নেব, তোমার কথা আমি ফেলতে পারব না।’
জেলখানায় দুই সপ্তাহ পরপর বাবার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি ছিল। বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্য বাড়িতে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হতো। যদিও ছোট ছিলাম, কিন্তু মনে আছে—দেখতাম, মা ছোট ছোট চিরকুট তৈরি করছেন। তখন বুঝতাম না, এগুলো কেন তৈরি হচ্ছে? মুখে সব কথা বলা যেত না বাবাকে। কারণ, তখন জেলখানায় অনেক পাহারা, অনেক চোখ চারদিকে। ঘরের ভেতরেই দুজন আইবির লোক টেবিলের ও-প্রান্তে বসে থাকত, আর আমরা বাবার পাশে।
আমাদের ভাইবোনদের দায়িত্ব ছিল হইচই করা। মা হইচইয়ের মধ্যেই বাবাকে যা বলার বলে ফেলতেন এবং চিরকুটগুলো দিয়ে দিতেন। খোকা চাচার দায়িত্ব ছিল আইবির লোকদের হাত দেখার নামে তাদের অন্যমনস্ক করে রাখা আর তাদের চা-নাশতা খাওয়ানো।
আগরতলা মামলা শুরুর আগে থেকেই আমার মায়ের ওপর কড়া নজরদারি শুরু হয়েছিল। অন্য সবাই মাকে না চিনলেও পাকিস্তান সরকার তাকে বিলক্ষণ চিনতে পেরেছিল। প্রায়ই মাকে জেরা করতে আইবি বা এসবি অফিসে যেতে হতো। একদিন তিনি জানতে পারলেন তাকেও বন্দি করা হবে। তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আমরা ছোট ছোট ভাইবোনেরা, আমার দাদি-দাদা—তাদের কী হবে? কে দেখাশোনা করবে? বিশেষ করে হাসিনা আপার। সেই পরিস্থিতিতে মা আপার বিয়ের কথা ভাবতে লাগলেন। আমার দাদা শেখ লুত্ফর রহমান একজন পাত্র পছন্দ করলেন প্রিয় পৌত্রীর জন্য। পাত্র সরকারি চাকুরে। সুপ্রতিষ্ঠিত সিএসপি অফিসার। কিন্তু মোনায়েম খানের ধমক খেয়ে পাত্রটি শেষমেশ বিয়েতে রাজি হলেন না। মার মনটা খুব ভেঙে গেল এবং খুব দুশ্চিন্তায় পড়লেন। ঠিক এর মধ্যেই মতিয়ুর রহমান সাহেব রংপুর থেকে এসে মাকে বললেন, ‘ভাবি, আপনি চিন্তা করবেন না। আমি একটা ছেলে ঠিক করেছি। নাম ড. ওয়াজেদ মিয়া। সদ্য বিলাতফেরত ছাত্রলীগ করা ছেলে। হাসিনার জন্য খুব ভালো পাত্র হবে।’ মা বাবাকে বিস্তারিত জানালেন। বাবা বললেন, ‘যেটা তুমি ভালো বোঝো, সেটাই করো।’
১৯৬৭ সালে ১৭ই নভেম্বর হাসিনা আপার কাবিন হয়ে গেল। বিশেষ অনুমতি নিয়ে জেলখানায় বাবা মেয়েজামাইকে দোয়া করলেন। জেলখানায় বসেই কন্যা সম্প্রদান করলেন। কারাগারের ভেতরে সে সময় একটা নতুন কামরা তৈরি হয়েছিল। জেল কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করল, বাবা যেন নতুন জামাইকে ওখানেই বরণ করেন। মিষ্টি ও ফুলের মালারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
প্রতি মাসে মা-সহ আমরা ভাইবোনেরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম, জেলখানায় বাবার সঙ্গে সাক্ষাতের দিনটির জন্য। এরকম একটা দিনে আমরা জেলখানায় গিয়ে বাবার সাক্ষাত্ পেলাম না। কারা কর্তৃপক্ষ বাবার অবস্থান সম্পর্কে কিছুই জানে না বলে জানাল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা জেলগেটে অপেক্ষা করলাম। আমাদের ঢুকতেও দেওয়া হলো না। অবশেষে আমরা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এলাম। দারুণ দুঃসময় তখন। বাবা বেঁচে আছেন কি না, বেঁচে থাকলে কোথায় আছেন—কিছুই জানি না। বেশ কয়েক মাস চলল এ অবস্থা। ছাত্রনেতাদেরও অনেকেই বন্দি। ৩২ নম্বরের বাড়ির সামনে মনে হয় কাকপক্ষীও ওড়ে না। এরপর ক্যান্টনমেন্টের ভেতরেই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার শুরু হলো। তারপর জানা গেল বাবাকে সেনানিবাসে নিয়ে বন্দি করে রাখা হয়েছে। জেল কর্তৃপক্ষ আসলেই জানত না, শেখ সাহেবকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সেনাবাহিনী? জানতেন না বাবাও। তবে এটা বুঝতে পেরেছিলেন, ভয়ানক বিপদ সামনে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বের হওয়ার পর গাড়িতে ওঠার আগে একমুঠো মাটি হাতে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বাবা বলেছিলেন, ‘আল্লাহ, আমার কবর যেন এই মাটিতেই হয়।’ এ কথাটা বাবার মুখে শোনা।
সেনানিবাসে ওরা বাবার ওপর অমানবিক মানসিক নির্যাতন করত। মাথার ওপরে সারাক্ষণ ৫০০ পাওয়ারের বাল্ব জ্বালিয়ে রাখত। একটু ঘুমিয়ে পড়লে বা ঝিমুনি এলে ডেকে তুলে দিত। মূলত মানসিক নির্যাতন করাটাই ছিল ওদের আসল উদ্দেশ্য। শেষের দিকে বিকেলে হাঁটার অনুমতি দিয়েছিল।
সেনানিবাসের দেওয়ালটা বেশি উঁচু ছিল না। আমরা প্রায়ই দুলাভাই, আপা, মা, ভাইবোনসহ আশপাশ দিয়ে গাড়িতে ঘুরতাম। যদি একটু চোখের দেখা পাই বাবার। কখনো কখনো দেখতেও পেতাম। প্রহরীরাও দেখে না দেখার ভান করত।
সেনানিবাসেই বাবার জীবননাশ হতে পারত। একদিন বাবা বিকেলে যখন হাঁটাহাঁটি করছিলেন ওখানকার একজন কর্মচারী বাবাকে জানালেন :‘স্যার, আপনি সন্ধের পর বাইরে হাঁটবেন না। এখানে একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে।’ ঠিক পরের দিন সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হয়। সেনানিবাসের ভেতরে প্রথমে গুলি, পরে বেয়নেট চার্জ করে। আসামি পালিয়ে যাওয়ার সময় গুলি করা হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয়।
সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যার খবরে সারা বাংলাদেশে আগুন জ্বলে উঠেছিল। আন্দোলন, প্রতিবাদে মানুষ তখন সেনানিবাসের দিকে ছুটছিল। স্লোগানে স্লোগানে তখন চারদিক মুখরিত। মানুষের মুখে মুখে তখন—‘জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব’, ‘মিথ্যা মামলা মানি না, মানব না’ স্লোগান। আন্দোলনের জোয়ারে আইয়ুব খান দিশেহারা। নতুন ফন্দি আঁটল গোলটেবিল বৈঠকের। কথা উঠল শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে সে বৈঠকে যোগদান করানোর। আওয়ামী লীগের কিছু বর্ষীয়ান নেতা, ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াসহ সবাই চাইছিলেন, বাবা যেন গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে সম্মতি দেন। আমাদেরও, বিশেষ করে আপা ও কামাল ভাইকে বলা হলো, আমরা যেন বাবার মুক্তি নেওয়ার ব্যাপারে সবাইকে বোঝাই। আপাকে ও কামাল ভাইকে শুনতে হলো :‘কেমন সন্তান তোমরা, বাবার মুক্তি চাও না?’ আমার মায়ের ওপর অনেক চাপ দিতে লাগল। কিন্তু মা তার সিদ্ধান্তে অনড়। বিনা শর্তে মিথ্যা মামলা তুলে নিতে হবে এবং প্রত্যেকে, যারা আব্বার সঙ্গে কারাবন্দি, তাদের সবাইকে বাবার সঙ্গেই বিনা শর্তে মুক্তি দিতে হবে। তবেই তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবেন।
মা নিজেই একদিন সশরীরে সেনানিবাসে গিয়ে দেওয়ালের এপাশ থেকে কথাটা আব্বাকে বললেন :‘তুমি কিছুতেই প্যারোলে মুক্তি নিয়ে বৈঠকে যেতে রাজি হবে না।’
কোনোভাবেই যখন মাকে বোঝানো বা রাজি করা যাচ্ছে না, তখন নেতারা অন্যপথে এগোতে চাইলেন। দু-এক দিন পরে, দুপুরবেলা আমি স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ব্যাগটা পাশে নামিয়ে রেখে বাড়ির সামনে এক্কা-দোক্কা খেলছি। হঠাত্ দেখি, নীল রঙের একটা টয়োটা গাড়ি এসে থামল আমাদের বাড়ির সামনে। তাতে বসে আছেন জুলফিকার আলি ভুট্টো সাহেব। পত্রপত্রিকায় ছবি দেখে তাকে খানিকটা চিনতাম। মায়ের মামাতো ভাই আকরাম মামা সেখানে ছিলেন। গাড়ি দেখেই মামা দৌড়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। মি. ভুট্টো গাড়ি থেকে নেমে আমার কাছে জানতে চাইলেন—কী নাম আমার, স্কুল থেকে ফিরলাম কি না ইত্যাদি। আমি সালাম দিয়ে উত্তর দিলাম। উনি জিজ্ঞাসা করলেন, মা কোথায়? ততক্ষণে তড়িঘড়ি করে আকরাম মামা ফিরে এসেছেন। আমি জবাব দেওয়ার আগেই আকরাম মামা বললেন, ‘উনি বাড়িতে নেই।’ ভুট্টো সাহেবের সঙ্গে আরো এক ভদ্রলোক ছিলেন। তাকে ডেকে ভুট্টো সাহেব বললেন, ‘হাসান, চলো যাই।’ আমাকে বাইবাই, খোদা হাফেজ বলে তারা চলে গেলেন। আমি বুঝতে পারলাম না এবং অনেকটা অবাক হয়ে গেলাম, মামা কেন ওদের এভাবে বললেন, মা বাড়িতে নেই?
ঘটনা হচ্ছে ভুট্টো সাহেবকে দেখেই মামা ছুটে রান্নাঘরে গিয়ে মাকে বললেন, ‘বুজি, ভুট্টো সাহেব এসেছেন।’ ঐ খবর শুনে মা তড়িঘড়ি করে পাশের বাড়ি চলে যান। ঐ বাড়িটি ছিল বদরুন্নেসা আহমেদের। তিনি ’৭২ সালে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। বদরুন্নেসা কলেজ ওনারই নামে।
দুই বাড়ির মধ্যে ছোট্ট একটা গেট ছিল। আমরা ওনাকে ফুফু বলে ডাকতাম। ঐ বাড়িতে ঢুকেই মা মামাকে বললেন, ‘বলে দে, আমি বাড়িতে নেই।’ মি. ভুট্টোর সঙ্গে দেখা করার প্রশ্নই ওঠে না। ভুট্টো সাহেব চলে গেছেন—এই খবর শুনে তবেই মা বাসায় ফিরে আসেন। ভুট্টো সাহেব নিশ্চয়ই খবর নিয়েই এসেছিলেন যে কাকে ধরতে হবে শেখ সাহেবকে বোঝানোর জন্য। কারণ, ভুট্টো সাহেব যা চাইবেন, তার সপক্ষে একটি কথা বলাও সম্ভব ছিল না মায়ের পক্ষে। বেগম মুজিব অনেক আগে থেকেই তার বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে।
এখানে বলতে হয়, কী অসাধারণ মনোবল ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল আমার মায়ের। তিনি জানতেন, জনতার সাগরে জেগেছে ঊর্মি এবং এও জানতেন, জনতা জেগে উঠলে কারো সাধ্য নেই তাকে থামানোর। সেটা জানবার জন্য নিশ্চয়ই তার উত্স ছিল এবং সেটাই স্বাভাবিক।
তার হাতেনাতে প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৬৯-এর ২২শে ফেব্রুয়ারি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত সবাইকে নিয়ে কারাগার থেকে সসম্মানে বেরিয়ে এলেন বাঙালির প্রিয় মুজিব ভাই, শেখ সাহেব, প্রাণের প্রিয় শেখ মুজিবুর রহমান।
বাবা জেলে থাকলে সব দিক সামলাতে হতো আমার মাকে। বাড়ির চারপাশে গুপ্তচররা নানান বেশে চলাফেরা করত। কখনো ফকির সেজে, পাগল সেজে, ফেরিওয়ালা সেজে এবং কখনো-বা বন্ধু সেজে। সেদিকেও মায়ের সদা সজাগ দৃষ্টি থাকত। আমাদের বাড়িতে ফেরিওয়ালা ঢোকা একদম নিষেধ ছিল। আমরা ভাইবোনেরা সবারই ডাকটিকিট সংগ্রহের নেশা ছিল। আমরা টিকিট সংগ্রহ করতাম ধানমন্ডি লেকের পাড়ে ফুটপাত থেকে। সেখানে হঠাত্ এক লোকের আবির্ভাব হলো। তিনি, আমরা যারা বাচ্চারা খেলতাম লেকের পাড়ে, তাদের নানা জিনিস দিতে শুরু করলেন। আমাকে লজেন্স ও ডাকটিকেট দিতেন। আমাকে ও জামাল ভাইকে বেশি বেশি দিতেন। আমরা দুই ভাইবোন খুশিতে বাসায় এসে একদিন মাকে সেগুলি দেখাতেই মা বললেন, ‘এক্ষুনি ফেরত দিয়ে এসো, অচেনা লোকের হাত থেকে কিছু নেবে না।’ আমরা দৌড়ে গিয়ে সেগুলি ফেরত দিয়ে এলাম। ঐ লোকটা আরেকটা কাজ করত। খুব দুঃখের কাহিনি শোনাত, তার নিজের জীবনের। সেটাও মাকে জানালাম। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কীভাবে যেন সেই লোকটা যে গুপ্তচর ছিল সেটা জানতে পারি। কারণ, আমি একবার যদি কারো চেহারা দেখতাম, সেটা ভুলতাম না।
গুপ্তচরবিষয়ক আরেকটা ছোট্ট ঘটনা। একবার এক লোক আমাদের বাড়ির সামনে বারবার সাইকেলে চড়ে চক্কর দিচ্ছিল। আমরা বাড়ির সামনে লেকের পাড়ে ভাইবোন ও পাড়ার ছেলেমেয়েরা বিকেলে খেলাধুলা করছি। ঐ লোককে সাইকেলে ঘোরাফেরা করতে দেখে কামাল ভাইয়ের সন্দেহ হলো। কামাল ভাই বললেন, এ নিশ্চয়ই এসবির লোক। জামাল ভাই, কামাল ভাই মিলে লোকটাকে জব্দ করার একটা ফন্দি আঁটলেন। আমাদের ‘টমি’ নামে বড়সড় একটা পোষা অ্যালসেসিয়ান কুকুর ছিল। জামাল ভাই, কামাল ভাই ওকে বলল—‘টমি ছুহ্।’ টমি তখন ভয়ংকরভাবে ছুটে গিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে করতে সাইকেলওয়ালার পেছন পেছন ছুটতে শুরু করল। লোকটা তাল সামলাতে না পেরে সাইকেল থেকে পড়ে গেল। টমিকে থামতে বলা হলো। ও মনিবের কথা শুনে ঘেউ ঘেউ করেই যাচ্ছিল। কিন্তু ঐ লোকের ওপর কোনো আক্রমণ করেনি। লোকটা সাইকেল নিয়ে কোনোক্রমে পালাতে পারলে বাঁচে। তবে যাওয়ার সময় জোরে জোরে বলে গেল—‘রাত কো দেখা দেঙ্গে।’ সেই রাতেই বাবা গ্রেফতার হলেন।
এসব দেখেশুনে মা আমাদের সবাইকে সাবধান হতে বললেন। অচেনা কারো সামনে কোনো কথা যেন না বলি। আরেকটা কাজ মা করতেন। যেদিন বাবার মিটিং থাকত, বাবাকে প্রস্তুত করে মিটিংয়ে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি নিজেই বেরিয়ে পড়তেন জনসভার উদ্দেশে। জনসভার চারপাশটা চক্কর দিয়ে আসতেন। নিজের চোখে সব দেখে আসতেন। লোক সমাগম কেমন হলো এবং লোকজনের মনোভাব সম্পর্কে তথ্য নিয়ে আসতেন। পাছে বাবাকে যাতে কেউ ভুল তথ্য দিতে না পারে। কেবল একটি বার এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছিল। সেবার তিনি জনসভার চারপাশে চক্কর দিতে যাননি। সেটা ছিল রেসকোর্স ময়দানে ৭ই মার্চ ১৯৭১-এর ঐতিহাসিক জনসভা।
আমাদের জীবনটা বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরপুর। এসব লিখেও শেষ করা যাবে না। আমাদের জীবনের সবচেয়ে মর্মান্তিক দিন, শুধু আমাদের নয়, গোটা বাঙালি জাতির জন্যও—১৫ই আগস্ট ১৯৭৫। ঐদিন আমাদের নিঃশেষ করে দিয়ে গেল ঘাতক-খুনিরা। আমরা শুধু দুটো বোন বেঁচে থাকলাম। আমরা বাকহীন, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম। এত বড় অন্যায়, কিছুতেই সহ্য হবে না। আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে নানান চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আজ আমরা দুটি বোন সত্যিকারের সোনার বাংলায় দাঁড়িয়ে আছি। হাসু আপা নিজের জীবনকে উত্সর্গ করে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার মানুষের কল্যাণের জন্য। সবার দোয়া ও ভালোবাসাই আমাদের পাথেয়। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
লেখক: শেখ রেহানা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ কন্যা